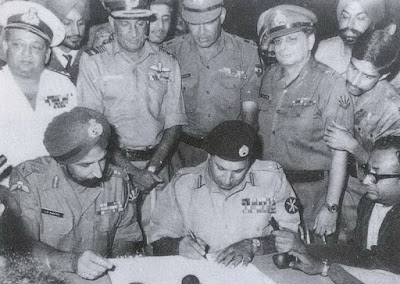তাই, ভাবছি, এই ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আগে-প্রকাশিত লেখাগুলি এবং নতুন কিছু লিখলে এখানে 'পুনঃপ্রকাশিত' করি। আজ 'নেতাজি সিরিজের' প্রথম রচনা। এ বছর অগস্ট মাসে 'ইতিহাস তথ্য ও তর্ক' ফেসবুক পত্রিকায় প্রকাশিত।
সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদ ও আজাদ হিন্দ সরকার
 |
| ভারতীয় সংবিধানের স্বচিত্র সংস্করণে আজাদ হিন্দ সংগ্রামকে স্মরণ। নন্দলাল বসু অঙ্কিত, ১৯৫০। বর্তমানে সংসদ ভবনের লাইব্রেরীতে হিলিয়াম কক্ষের মধ্যে সংরক্ষিত। |
ভাষা নিয়ে নেতাজির বৃহৎ চিন্তাভাবনায় কিছু আলোকপাত করা যাক । যেমন, 'আজাদ হিন্দ' পত্রিকা। জার্মানির ফ্রি ইন্ডিয়া সেন্টার থেকে ইংরেজি ও জার্মান দুই ভাষায় প্রকাশিত হত (আজ নেতাজি রিসার্চ ব্যুরোতে সংখ্যাগুলি সংরক্ষিত)।তবে আরো গুরুত্বপূর্ণ ছিল আজাদ হিন্দ রেডিও। সাতটি ভারতীয় ভাষায় দৈনিক সম্প্রচার চলত - হিন্দুস্তানী, বাংলা, তামিল, তেলুগু, গুজরাটি, ফার্সি আর পুশতু । আর নেতাজির ইংরেজি আর হিন্দুস্তানি ভাষণ সঙ্গে সঙ্গে তামিলে অনুবাদিত হয়ে পুনঃপ্রচারিত হত ৮,৯।যেমন প্রভিশনাল সরকারের ঘোষণা পত্র ইংরিজি, হিন্দুস্তানি ওঃ তামিল ভাষায় প্রচারিত হয়েছিল । হিসেবটা সোজা - সবার ভাষাকে সম্মান না করলে একসঙ্গে সংগ্রাম হবে কি করে? প্রকৃত নেতার এই বৈশিষ্ট্য - কাউকে দূরে ঠেলে দেন না, সবাইকে নিয়ে চলার চেষ্টা করেন।
তবে শুধু ভাষা নয়, স্বাধীন ভারতে কি ধরণের লিপি ব্যবহার হবে তা নিয়েও নেতাজি পরিকল্পনা করেছিলেন। দেবনাগরী ও আরব-ফার্সি দুই লিপি উপকারিতা স্বীকার করেও তিনি কংগ্রেস সভাপতি রূপে তাঁর বিখ্যাত হরিপুরা কংগ্রেস ভাষণে একটি অভিনব প্রস্তাব করেছিলেন - বলেছিলেন যে রোমান লিপিতে হিন্দুস্তানী একটি সর্বভারতীয় মাধ্যম হতে পারে ১০। এই ব্যাপারে নেতাজির ওপর আধুনিক তুরস্কের জাতির জনক মুস্তাফা কেমাল আতাতুর্ক'র প্রভাব লক্ষণীয় । ১৯২০র দশকে একই ভাবে আতাতুর্ক তুরস্কে রোমান লিপির জন্যে সর্বশিক্ষা অভিযান শুরু করেন । সুভাষ চন্দ্র আতাতুর্ক'র দেশ গঠনের নানারকম পরিকল্পনার গুনগ্রাহী ছিলেন। তাঁর লেখায় ও ভাষণে একাধিকবার এর প্রমান পাওয়া যায় ১১ ।
সেনাবাহিনী - আজাদ হিন্দ ফৌজ
অস্থায়ী ভারত সরকারের সেনাবাহিনীর নামের সঙ্গে আমরা সবাই পরিচিত - ইন্ডিয়ান ন্যাশানাল আর্মি বা আজাদ হিন্দ ফৌজ । সঠিক সৈন্যসংখ্যা নিয়ে দ্বিমত থাকলেও তিনটি সামরিক ডিভিশনে আনুমানিক ৪৫ থেকে ৫০ হাজার আজাদী সৈন্য ছিলেন।এছাড়া আরো পাঁচ ডিভিশন সৈন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। এর মধ্যে প্রথম INA ডিভিশন'র অধীনস্ত ছিল ইতিহাসে-বিখ্যাত গান্ধী ব্রিগেড, নেহেরু ব্রিগেড ও আজাদ ব্রিগেড ১২,১৩। দেশীয় আন্দোলনের সঙ্গে সংযোগ দেখাতে সদা -আগ্রহী নেতাজি তাঁর প্রধান ব্রিগেডেদের নামকরণ করেছিলেন দেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় তিন নেতার নামে #।
ক্যাবিনেটে সদস্য ছিলেন -
সুভাষ চন্দ্র বসু - রাষ্ট্রপ্রধান, প্রধানমন্ত্রী, যুদ্ধ ও বিদেশ মন্ত্রক । **
লেঃ কর্নেল এ সি চ্যাটার্জি (পরে এন. রাঘবন) - অর্থ মন্ত্রক ।
ডঃ: লক্ষী স্বামীনাথন - মহিলা বিষয়ক মন্ত্রক (minister for women affairs )
এ এম সহায় - প্রধান সচিব
এস এ আয়ার - প্রচার ও জন সংযোগ মন্ত্রক।
রাসবিহারী বসু - সর্বোচ্চ উপদেষ্টা (আজাদ হিন্দের সংগ্রাম এবং পুরোনো বিপ্লবীরা যেন একই পথের পথিক)
করিম গিয়ানি , জন থিবি , দেবনাথ দাস, সর্দার ইশার সিংহ, ডি.এম. খান, আত্তাভার য়েলাপ্পা - বর্মা , থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর এবং হংকং থেকে উপদেষ্টা।
লেঃ কর্নেল জে কে ভোঁসলে , লেঃ কর্নেল গুলজারা সিং , লেঃ কর্নেল শাহ নাওয়াজ খান , লেঃ কর্নেল আজিজ আহমেদ, লেঃ কর্নেল মোহাম্মদ জামন কিয়ানি, লেঃ কর্নেল এন.এস. ভগত, লেঃ কর্নেল এহসান কাদির এবং লেঃ কর্নেল এ.সি লোগানাথান - আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রতিনিধি।
এ এন সরকার - আইন বিষয়ক উপদেষ্টা ২২,+।
আবিদ যোগ করতে ভোলেননি, ''আমাদের সবার কিন্তু নিজ নিজ ধর্ম এবং নিজস্ব ভাষা ছিল। কিন্তু, রাজনৈতিক লক্ষে আমরা ছিলাম এক, প্রতিজ্ঞাবদ্ধ এবং অবিভাজ্য ।'' নেতাজি তাঁদের কাউকেই নিজের ধর্ম, সংস্কৃতি, ভাষা ত্যাগ করতে বলেননি। তবে এই সব পরিচয়ের উর্ধে যে দেশের পরিচয়(identity) সেই পরিচয়ের জন্যে একত্র হতে বলেছিলেন। জাতীয় ঐক্যের ব্যাপার সবার ওপরে এবং সেখানে তিনি অনমনীয়। যেমন, রেঙ্গুনের ধনী দক্ষিণ ভারতীয় চেট্টিয়ার সম্প্রদায় ছিলেন আজাদ হিন্দ সরকারের বড় পৃষ্টপোষক। তাঁদের প্রধান মন্দিরে official visit করলে আর্থিক সমর্থন আরো বাড়বে, এটাই অনুমেয়। নেতাজি কিন্তু স্পষ্ট জানিয়ে দেন যে মন্দিরের পুরোহিতগণ যদি তাঁর ক্যাবিনেটের হিন্দু ও ও-হিন্দু সকল মন্ত্রীকে মন্দিরে প্রবেশ করতে দেন তবেই তিনি যাবেন! আমরা- ওরা কোনোমতেই চলবে না। শেষ পর্যন্ত চেট্টিয়ার মন্দির কর্তৃপক্ষ সবাইকে আমন্ত্রণ জানান। হিন্দু-মুসলমান-শিখ-ক্রিস্টান সকল ভারতীয় মিলে সেদিন এক আশ্চর্য জনসমাগম হয়েছিল ২৪।
মনে রাখা আবশ্যক, নেতাজি কিন্তু ভগৎ সিং, চদ্রশেখর আজাদ'র মত ঘোষিত-নাস্তিক, কিংবা জওহরলাল নেহরুর মত এগ্নস্টিক ছিলেন না। বিশ্বজননী-রূপে তিনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করতেন। যুদ্ধের ভয়ানক ব্যস্ততার মধ্যে সারাদিনের কাজের শেষে অনেক রাত্রে সিঙ্গাপুরের রামকৃষ্ণ মিশনে গিয়ে মিলিটারি পোশাক ছেড়ে একটি সিল্কের ধুতি পরে ঘন্টা দুই ধ্যানমগ্ন হতেন। এই ছিল তাঁর 'রিচার্জ' ২৫। তবে সেটা তাঁর ব্যক্তিগত জীবন। আয়ার'র বর্ণনা থেকে আমরা জানতে পারি , '' একদিনের জন্যেও তাঁকে দেখিনি প্রকাশ্যে, জনসমক্ষে কোনো ধার্মিক আচরণ করতে। তাঁর কর্মই ছিল তাঁর ধর্ম, জীবনের প্রতি মুহূর্ত সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে সেই ধর্ম তিনি পালন করতেন''২৬ । এবং এই জীবনাদর্শ ও বিশ্বব্যাপী অভিজ্ঞতা থেকেই আসে আজাদ হিন্দ সরকারের ঘোষণাপত্রের শেষ অনুচ্ছেদে নেতাজির দ্যর্থহীন ঘোষণা - ''...[স্বাধীন ভারতের অস্থায়ী সরকার] প্রত্যেক ভারতবাসীকে নিজ নিজ ধর্ম পালন করার স্বাধীনতা দিতে অঙ্গীকারবদ্ধ , এবং সবাইকে সমান অধিকার ও সুযোগসুবিধা প্রদান করতেও দ্বায়িত্ববদ্ধ । বিদেশী ঔপনিবেশিক সরকারের দ্বারা প্রতিপালিত সব ভেদ, দূরত্ব ও তফাৎ'র উর্ধে গিয়ে প্রত্যেক ভারতীয়ের সুখ ও সমৃদ্ধির জন্যে সংগ্রাম করা এই সরকারের প্রথম এবং প্রধান কাজ হবে ।'' ২৭
টিকা
*সিঙ্গাপুর ছেড়ে যাওয়ার কয়েকদিন আগে নেতাজি তাঁর বিশ্বস্ত অফিসার সিরিল জন স্ট্রেসিকে নির্দেশ দেন, আজাদ হিন্দের শহীদ সৈন্যদের জন্যে একটি স্মৃতিস্তম্ভ তৈরী করতে হবে। অল্প কয়েকদিনেই মধ্যেই সিঙ্গাপুরের সমুদ্রতটে স্ট্রেসি যে সৌধ নির্মাণ করেন তাতে খোদাই করা ছিল এই motto। কিন্তু, চরম অনৈতিকভাবে বিজয়ী মিত্রশক্তি সেই সৌধ ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দেয়! বহু দশক পরে সিঙ্গাপুরে বসবাসকারী কয়েকজন ভারতীয় একটি আধুনিক সৌধ করেছেন ; আরেকটি প্রতিরূপ আছে কলকাতার নেতাজি ভবনে।
গান্ধীজি প্রসঙ্গে বলা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক যে স্বাধীন ভারত কোনোদিন সরকারিভাবে তাঁকে 'জাতির জনক' উপাধি দেয়নি। এই সম্মানের উৎস নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু'র আজাদ হিন্দ রেডিও ভাষণ(৬ই জুলাই, ১৯৪৪)। শুধু তাই নয়, পুনার জেলে কস্তুরবা গান্ধীর মৃত্যর পরে বেতার ভাষণে নেতাজি সেই অসামান্যা নারীকে 'mother of the Indian people' বলে অভিহিত করেন।
^ সব অনাবাসী ভারতীয় যে টাকা পয়সা দিতে অতটা উৎসাহী ছিলেন না। শেষ পর্যন্ত আজাদ হিন্দ সিদ্ধান্ত নেয় যে অনিচ্ছুকরা ১০% দিলেই হবে।
** তাহলে কি নেতাজি ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী? না , কারণ নেতাজি তাঁর ভাষণে নিজেই স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে আজাদ হিন্দ হল 'অস্থায়ী সরকার ', এবং ভারত স্বাধীন হবার পরেই এই সরকারের কাজ শেষ। তারপরে কি সরকার গঠিত হবে তা ঠিক করবেন স্বাধীন ভারতের মানুষ।
+ জার্মানি, ইতালি, জাপান ও অক্ষশক্তি-সমর্থিত ৬টি সরকার আজাদ হিন্দকে স্বীকৃতি দিয়েছিল। আয়ারল্যান্ডের রাষ্ট্রপতি ইমন ডি'ভালেরা শুভেচ্ছা বার্তা পাঠিয়েছিলেন।
সহায়ক গ্রন্থ
১,২,৩ - Sugata Bose, His Majesty 's Opponent, 2011, Penguin Books p. 210, 257, 299
৪ - শিশির কুমার বসু, বসুবাড়ি, ১৯৮৫, আনন্দ পাবলিশার্স , পৃ.৮২-৮৩
৫, ৬ - Leonard Gordon, Brothers against the Raj, 1990, Rupa Publications, pp. 459-460; Bose, His Majesty 's Opponent, 2011, Penguin Books pp.210-211
৭ - https://www.youtube.com/watch?v=9Cn34HFZ8tc
৮, ৯ - Leonard Gordon, Brothers against the Raj, 1990, Rupa Publications, p. 454-455; Sugata Bose, His Majesty 's Opponent, 2011, Penguin Books p. 225, 245
১০ - Sugata Bose, His Majesty 's Opponent, 2011, Penguin Books p. 140; Crossroads, being the works of Subhas Chandra Bose 1938-40, published by Netaji Research Bureau, 1962, Asia Publishing House. pp.13-14
১১- Congress President: Speeches, Articles, and Letters January 1938–May 1939, p. 61; Hugh Toye, The Springing Tiger, Jaico Publishing House, p. 179.
১২, ১৩ - Leonard Gordon, Brothers against the Raj, 1990, Rupa Publications, p. 498; Sugata Bose, His Majesty 's Opponent, 2011, Penguin Books pp.251-252
১৪- Sugata Bose, His Majesty 's Opponent, 2011, Penguin Books p.275
১৫, ১৬ - Leonard Gordon, Brothers against the Raj, 1990, Rupa Publications, p. 496-497; Sugata Bose, His Majesty 's Opponent, 2011, Penguin Books p.246-247; William L. Shirer, Rise and Fall of the Third Reich, 1960, Arrow Books, p. 975
১৭ - https://en.wikipedia.org/wiki/Sher-e-Hind ; https://en.wikipedia.org/wiki/Sardar-e-Jung
১৮, ১৯ - Leonard Gordon, Brothers against the Raj, 1990, Rupa Publications, p. 510; Sugata Bose, His Majesty 's Opponent, 2011, Penguin Books p.272-73
২০- https://www.facebook.com/.../permalink/715524075604174/
২১ - Leonard Gordon, Brothers against the Raj, 1990, Rupa Publications, p. 502, Unto Him a Witness, SA Ayer, 1951, Thacker and Co Ltd, p. 249
২২ - Selected speeches by Subhas Chandra Bose, introduction by S.A. Ayer, Publications Division, Ministry of Information and Broadcasting, Government of India. pp. 219-220; Sugata Bose, His Majesty 's Opponent, 2011, Penguin Books p.255
২৩-Sugata Bose, His Majesty 's Opponent, 2011, Penguin Books pp.281-82
২৪ -Sugata Bose, His Majesty 's Opponent, 2011, Penguin Books p.256
২৫-Leonard Gordon, Brothers against the Raj, 1990, Rupa Publications, p.502;
Sugata Bose, His Majesty 's Opponent, 2011, Penguin Books p.253
২৬- Unto Him a Witness, SA Ayer, 1951, Thacker and Co Ltd, p. 269
২৭-Selected speeches by Subhas Chandra Bose, introduction by S.A. Ayer, Publications Division, Ministry of Information and Broadcasting, Government of India. pp. 218-220